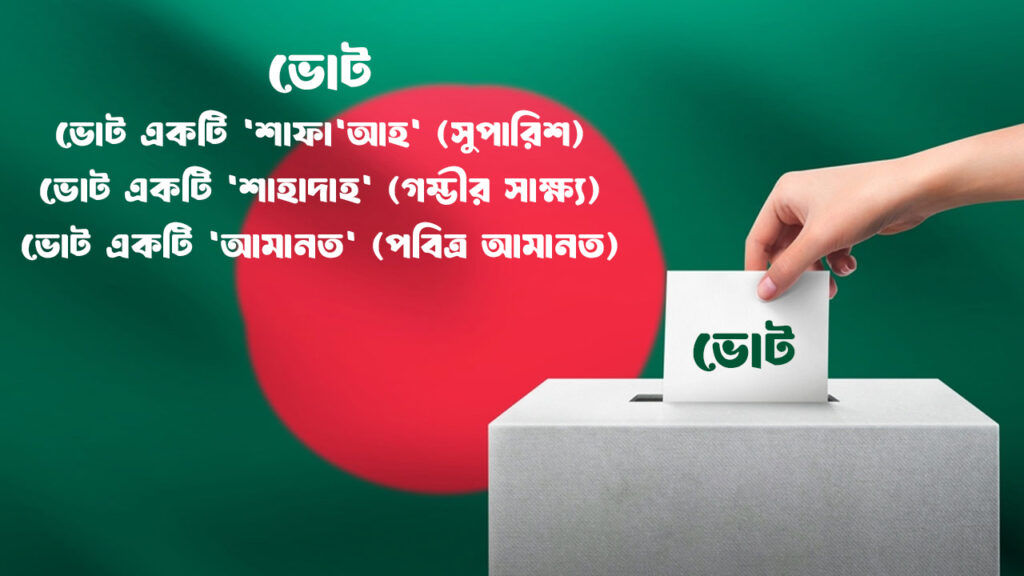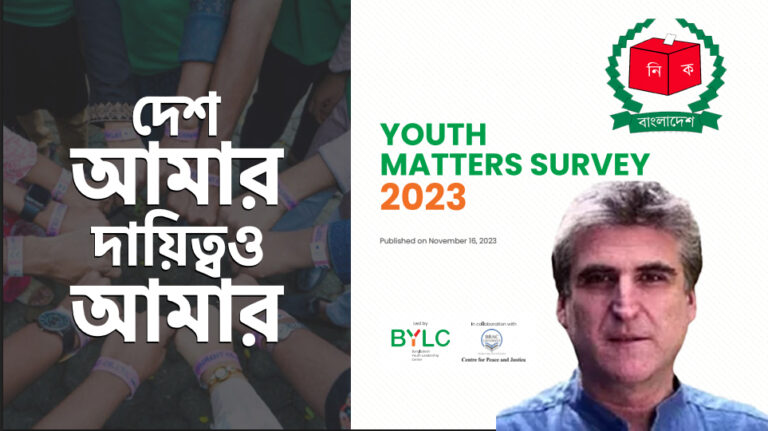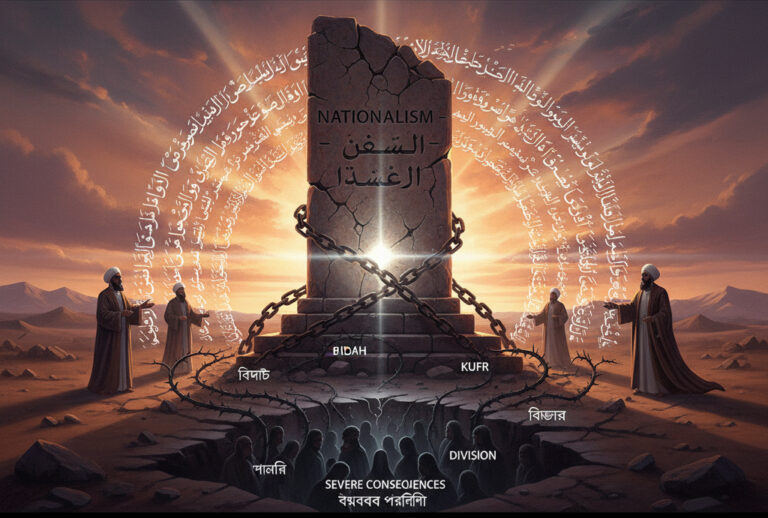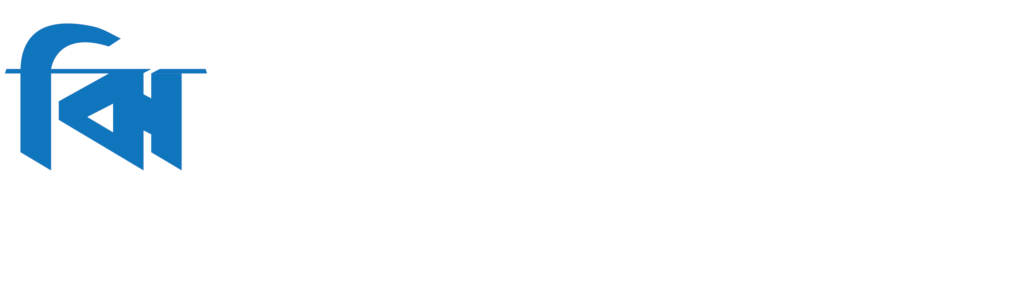শেখ জিল্লুর রহমান
ভোটের তাৎপর্য: আমানত, সাক্ষ্য ও সুপারিশ হিসেবে একজন মুসলমানের নাগরিক দায়িত্ব নিয়ে ইসলামী বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একজন মুসলিম নাগরিকের অবস্থান এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে ভোটাধিকার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এই প্রেক্ষাপটে, ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটের গুরুত্ব নিছক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্যতা খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি এক গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যালোচনার দাবি রাখে। ইসলামে একজন মুসলমান কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, তা তার বিশ্বাসের মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। এই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য হলো, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভোট কেবল রাজনৈতিক পছন্দের প্রকাশ নয়, বরং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ, যার প্রভাব ইহকাল ও পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি ভোট একই সঙ্গে একটি পবিত্র আমানত (Amanah), একটি seria সাক্ষ্য (Shahadah) এবং একটি সুদূরপ্রসারী সুপারিশ (Shafa’ah) – এই তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একজন মুসলমানের নাগরিক দায়িত্বের ওপর তাদের সম্মিলিত প্রভাব বিশ্লেষণ করাই এই প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য। সঠিক নিয়ত ও ইসলামী নৈতিকতা অনুসরণের মাধ্যমে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া, প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে ভোট প্রদান পর্যন্ত, একটি ইবাদতে পরিণত হতে পারে ।
ইসলামে শাসন ও নেতৃত্বের মৌলিক নীতিমালা
ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা মানবসৃষ্ট কোনো তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ঐশী নির্দেশনার ওপর। কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত নীতিমালাই এ ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি।
শূরা বা পরামর্শের নীতি
ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো শূরা বা পারস্পরিক পরামর্শের নীতি। এটি কোনো নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক মডেল নয়, বরং একটি অপরিহার্য ঐশী নির্দেশনা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “…এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।” (সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৮)। অন্যত্র আল্লাহ তাঁর রাসুল (সা.)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, “আর কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।” (সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯)। এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ করা ইসলামের এক অলঙ্ঘনীয় বিধান । আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট প্রদানকে এই শূরার নীতির একটি প্রায়োগিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।
খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন: একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন পদ্ধতি শূরার নীতির সর্বোত্তম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রত্যেকটির মূলে ছিল পরামর্শ, যোগ্যতা যাচাই এবং জনগণের সম্মতি।
হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছিল সাকিফা বনু সায়েদা নামক স্থানে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের পর। সেখানে উমর (রা.) কর্তৃক হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব এবং উপস্থিত সাহাবিদের সর্বসম্মত সমর্থনের (বায়’আত) মাধ্যমে তিনি প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন । হযরত উমর (রা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.) মনোনয়ন দিলেও সেই মনোনয়ন কার্যকর হয়েছিল জনগণের সম্মতির পর। হযরত উসমান (রা.) নির্বাচিত হয়েছিলেন হযরত উমর (রা.) কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্যের একটি শূরা বা কমিটির মাধ্যমে, যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একজনকে খলিফা হিসেবে চূড়ান্ত করেন । এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, নেতা নির্বাচনের ইসলামী পদ্ধতি স্বৈরতান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক নয়, বরং তা পরামর্শভিত্তিক এবং এতে সমাজের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মতামত ও সাধারণ জনগণের সম্মতির গুরুত্ব অপরিসীম ।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আহলুল হল ওয়াল আকদ বা সমাজের প্রভাবশালী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শে নেতা নির্বাচিত হতেন। আধুনিক যুগে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের বিশাল পরিসরে সেই পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত নীতি—অর্থাৎ জনগণের সম্মতির মাধ্যমে নেতাকে বৈধতা দেওয়া—আজও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে সেই শূরার নীতির একটি প্রায়োগিক রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যেক ভোটার নিজেই একজন আহলুল হল ওয়াল আকদ-এর ভূমিকা পালন করে।
ইসলামে নেতার অপরিহার্য গুণাবলি
ইসলামে নেতা নির্বাচন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। একজন ভোটারকে অবশ্যই প্রার্থীর মধ্যে কিছু মৌলিক গুণাবলি সন্ধান করতে হবে। এই গুণাবলিগুলোই নির্ধারণ করে একজন শাসক ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম কি না।
| গুণাবলি | নেতৃত্বের প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞা | কোরআনের উদ্ধৃতি | হাদিসের উদ্ধৃতি |
| তাকওয়া (আল্লাহভীতি) | শাসকের সকল কাজে আল্লাহর প্রতি জবাবদিহিতার ভয় রাখা, যা তাকে স্বৈরাচার ও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখে। | “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি।” (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩) | “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।” (বুখারি: ৩৫৫৯) |
| আদল (ন্যায়পরায়ণতা) | ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আত্মীয়-শত্রু নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠা করা। | “নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, দয়া ও আত্মীয়-স্বজনকে (তাদের হক) প্রদানের হুকুম দেন।” (সূরা নাহল ১৬:৯০) | “কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হবে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক।” (তিরমিজি: ১৩২৯) |
| আমানতদারিতা (বিশ্বস্ততা) | জনগণের সম্পদ, ক্ষমতা ও অধিকারকে পবিত্র আমানত হিসেবে রক্ষা করা এবং খেয়ানত না করা। | “নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে।” (সূরা নিসা ৪:৫৮) | “যার আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই।” (মুসনাদে আহমদ: ১২৫৬৭) |
| ইলম (জ্ঞান) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) | রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দূরদৃষ্টি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা। | “আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কাজে নিযুক্ত করুন। আমি রক্ষণাবেক্ষণ ভালো পারি এবং এ কাজের পূর্ণ জ্ঞান রাখি।” (সূরা ইউসুফ ১২:৫৫) | “জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।” (আল-মাকাসিদ আল-হাসানাহ) |
| রহমত (দয়া ও সহানুভূতি) | জনগণের প্রতি কঠোর না হয়ে স্নেহশীল, দয়ালু ও কল্যাণকামী হওয়া। | “আপনি যদি কর্কশভাষী ও কঠোর স্বভাবের হতেন, তবে লোকেরা আপনার আশপাশ থেকে চলে যেত।” (সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯) | “তিনি (রাসুল) তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।” (সূরা তাওবা ৯:১২৮) |
| শূরাভিত্তিক মনোভাব | গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, একনায়কতান্ত্রিক না হওয়া। | “…এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।” (সূরা আশ-শূরা ৪২:৩৮) | “রাসুল (সা.) অপেক্ষা অধিক নিজের সাথিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আমি কাউকে দেখিনি।” (তিরমিজি: ১৭১৪) |
নেতার জন্য নির্ধারিত এই গুণাবলিগুলো কেবল একটি আদর্শ তালিকা নয়, বরং এটি ভোটারের জন্য একটি দায়িত্বের চেকলিস্ট। এই গুণাবলি উপেক্ষা করে কেবল ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ভোট দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে এক ধরনের কর্তব্য অবহেলা।
ভোট একটি ‘আমানত’ (পবিত্র আমানত)
ইসলামে ‘আমানত’ শব্দটি শুধুমাত্র গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ ফেরত দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি ব্যাপক ধারণা, যা মানুষের ওপর অর্পিত সকল প্রকার দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষের জীবন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জ্ঞান, গোপনীয়তা এবং সর্বোপরে জনগণের পক্ষ থেকে অর্পিত ক্ষমতা ও পদমর্যাদা—এ সবই আমানত ।
আমানত রক্ষার কোরআনিক নির্দেশ
সূরা আন-নিসার ৫৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা’আলা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে।” ।
এই আয়াতটি ভোটের ইসলামী ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে ‘আমানত’ হলো শাসন করার পবিত্র দায়িত্ব এবং ‘আহলিহা’ বা ‘হকদার’ হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার মানদণ্ডে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। সুতরাং, একজন নাগরিকের ভোট হলো সেই আমানতকে তার যোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যম। এটি কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নয়, বরং একটি সম্মিলিত দায়িত্ব। প্রত্যেক ভোটার সমাজের পক্ষ থেকে একজন আমানতকারী বা ট্রাস্টি।
খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণতি
এই আমানতের খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামে একটি ভয়াবহ পাপ। রাসুলুল্লাহ (সা.) খেয়ানতকে মুনাফিকের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । হাদিসে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে: “যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই” । এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও সতর্কতামূলক হাদিসটি হলো, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, “যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।” পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, “আমানত কীভাবে নষ্ট হবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো” । এই হাদিসটি সরাসরি অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে। এটি নিছক একটি ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি এমন এক সামাজিক অবক্ষয়ের চিহ্ন, যা কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
আমানতের ধারণাটি ভোটকে একটি пассив পছন্দ থেকে একটি সক্রিয় দায়িত্ব পালনে রূপান্তরিত করে। ভোটার কেবল কাউকে ‘পছন্দ’ করছেন না, বরং তিনি সমাজের নিরাপত্তা, সম্পদ এবং ভবিষ্যৎ সেই ব্যক্তির হাতে অর্পণ করছেন। এই অর্পণের কাজটি অবশ্যই জেনে-বুঝে এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে করতে হবে। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, আমানত তার যোগ্য প্রাপকের (আহল) কাছেই পৌঁছে দিতে হবে। সুতরাং, যে ভোটার প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই না করে বা জেনেশুনে কোনো দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে ভোট দেয়, সে কোরআনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে এবং এক মহাপাপে লিপ্ত হয়।
ভোট একটি ‘শাহাদাহ’ (গম্ভীর সাক্ষ্য)
ইসলামের নৈতিক ও আইন ব্যবস্থায় ‘শাহাদাহ’ বা সাক্ষ্য প্রদানের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্য প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার এটিই প্রধান মাধ্যম।
ভোটার একজন সাক্ষী
যখন একজন নাগরিক ভোট প্রদান করেন, তখন তিনি মূলত একটি সাক্ষ্য দেন। তার ভোট এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই প্রার্থী চরিত্র, যোগ্যতা ও সততার দিক থেকে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার এবং এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করার যোগ্য।” এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ভোট প্রদান একটি অত্যন্ত গম্ভীর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ।
সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে কোরআনের কঠোর নির্দেশনা
পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং আপোসহীন নির্দেশনা দিয়েছে।
- সূরা আন-নিসা, আয়াত ১৩৫: এই আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন:
“হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।” । এই আয়াতটি পরিবার, বংশ বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ভোট দেওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। সাক্ষ্য বা ভোট অবশ্যই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে হতে হবে।
- সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ৮: এই আয়াতে বলা হয়েছে:
“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর।” । এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের পরিপূরক। কোনো প্রার্থী বা দলের প্রতি বিদ্বেষবশত তাকে ভোট না দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া নিষিদ্ধ। ন্যায়বিচারকে ব্যক্তিগত অনুভূতির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।
মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতা
যদি ভোট একটি সাক্ষ্য হয়, তবে জেনেশুনে একজন অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ বা অত্যাচারী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া ‘শাহাদাত আয-যূর’ বা মিথ্যা সাক্ষ্যের শামিল। এটি ইসলামে একটি কবিরা গুনাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরক এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতার মতো মহাপাপের সঙ্গে উল্লেখ করে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মতকে বারবার সতর্ক করেছেন । এই তুলনাটি একজন মুসলমানের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট যে, একটি অসৎ ভোট তাকে কতটা আধ্যাত্মিক বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। একইভাবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করাও একটি বড় পাপ । যখন একজন যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে একজন অযোগ্য প্রার্থীকে পরাজিত করা সম্ভব, তখন ভোটদানে বিরত থাকা সত্যকে গোপন করার নামান্তর।
ইসলামী আইন অনুযায়ী, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ‘ইলম’ বা জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। যা জানা নেই, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যায় না । এর একটি গভীর তাৎপর্য হলো, একজন অজ্ঞ ভোটারের ভোট একটি অবৈধ সাক্ষ্য। যে ভোটার প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ড, চরিত্র ও নীতি সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে ভোট দেয়, সে মূলত এমন একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যা সম্পর্কে সে অবগত নয়। এটি একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং পাপপূর্ণ কাজ।
একটি মিথ্যা ভোটের মাধ্যমে তিন পক্ষের ওপর জুলুম করা হয়: (১) অযোগ্য প্রার্থীর ওপর, কারণ তাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হলো যা ব্যবহার করে সে নিজের পরকালীন ধ্বংস ডেকে আনবে; (২) যোগ্য প্রার্থীর ওপর, যার অধিকার হরণ করা হলো; এবং (৩) পুরো সমাজের ওপর, কারণ তাদের একজন অযোগ্য শাসকের অধীনে কষ্ট পাওয়া হবে । এই ত্রিবিধ জুলুমের ধারণাটি একটি ভুল ভোটের পাপকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।
ভোট একটি ‘শাফা’আহ’ (সুপারিশ)
ইসলামে ‘শাফা’আহ’ বা সুপারিশের ধারণাটি দায়িত্বের অংশীদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সূরা আন-নিসার ৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন:
“যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তার সওয়াবের একটি অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করবে, সে তার পাপের একটি অংশ পাবে। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর নজর রাখেন।” ।
নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শাফা’আতের প্রয়োগ
রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভোট হলো সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারিশ।
- উত্তম সুপারিশ (শাফা’আহ হাসানাহ): একজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু প্রার্থীকে ভোট দেওয়া একটি উত্তম সুপারিশ। এই সুপারিশের ফলে নির্বাচিত নেতা যত ভালো কাজ করবেন—যেমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণের সেবা, দেশের উন্নয়ন—তার সওয়াবের একটি অংশ ভোটারও পেতে থাকবেন । এই সওয়াব একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা নেতার कार्यकाल পর্যন্ত জারি থাকে।
- মন্দ সুপারিশ (শাফা’আহ সাইয়্যি’আহ): বিপরীতভাবে, একজন দুর্নীতিবাজ, অত্যাচারী বা অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া একটি মন্দ সুপারিশ। এর ফলে সেই নেতা যত অন্যায়, জুলুম ও দুর্নীতি করবেন, তার পাপের একটি অংশ বা বোঝা সুপারিশকারী বা ভোটারকেও বহন করতে হবে । আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পালানোর কোনো পথ নেই, কারণ তিনিমুকীত—সর্ববিষয়ের পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী।
এই আয়াতটি আধুনিককালেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীসহ অনেক সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ভোটের গুরুত্ব বোঝাতে এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন, যা প্রমাণ করে এর আবেদন চিরন্তন ।
‘শাফা’আহ’-এর এই নীতি ভোটকে একটি এককালীন কাজ থেকে একটি চলমান পুরস্কার বা পাপের স্রোতে পরিণত করে। এটি এমন কোনো কাজ নয় যা সম্পন্ন করার পর ভুলে যাওয়া যায়। ভোটার কেবল নির্বাচনের দিনের জন্য দায়ী নন, বরং তার সুপারিশের ফলে নির্বাচিত নেতার পুরো শাসনকালের কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য। যদিও নিয়ত বা উদ্দেশ্য একটি কাজের ভিত্তি, কিন্তু ‘শাফা’আহ’-এর নীতি প্রমাণ করে যে, কাজের ফলাফলও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো নিয়ত করে অবহেলাবশত একজন খারাপ প্রার্থীকে ভোট দিলে, সেই খারাপ ফলাফলের বোঝা ভোটারকে বহন করতে হবে। সুতরাং, ভালো নিয়তের সঙ্গে অবশ্যই যথাযথ সতর্কতা ও বিচার-বিবেচনা যুক্ত হতে হবে।
মুসলমানের বাস্তব দায়িত্ব ও চূড়ান্ত জবাবদিহিতা
আমানত, শাহাদাহ ও শাফা’আহ—এই তিনটি ধারণা একত্রিত হয়ে একজন মুসলমানের ওপর এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করে, আর তা হলো একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল ভোটার হওয়া। এই তিনটি দায়িত্ব পালনের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞান ও সচেতনতা।
ব্যবহারিক দায়িত্ব ও ‘অপেক্ষাকৃত কম মন্দের’ নীতি
বাস্তব জীবনে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যেখানে কোনো প্রার্থীই ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আদর্শ না। এক্ষেত্রে ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্রের একটি নীতি হলো ইখতিয়ার আখাফফ আদ-দারারাইন অর্থাৎ দুটি মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দটিকে বেছে নেওয়া। অনেক ইসলামি পণ্ডিত, যারা গণতন্ত্রের সমালোচক, তারাও বৃহত্তর ক্ষতি থেকে বাঁচতে বা মুসলিমদের জন্য উল্লেখযোগ্য কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে ভোট দেওয়াকে জায়েজ মনে করেন ।
উদাসীনতা ও ভোট বর্জনের বিপদ
পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ভোটদানে বিরত থাকা বা উদাসীনতা কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নয়। যখন একজন অত্যাচারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে একজন অপেক্ষাকৃত ভালো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বড় ধরনের জুলুম প্রতিহত করার সুযোগ থাকে, তখন ভোটদানে বিরত থাকা সেই জুলুমকে নীরবে সমর্থন করার শামিল। এটি আমানত রক্ষায় ব্যর্থতা, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গোপন করা এবং একটি মন্দ সুপারিশকে জয়ী হতে দেওয়ার নামান্তর।
পরকালীন জবাবদিহিতা
সর্বোপরি, প্রত্যেক মানুষকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে । রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তার জীবন, জ্ঞান, সম্পদ এবং শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে । ভোট যেহেতু ক্ষমতা ও দায়িত্বের একটি অংশ, তাই এ বিষয়েও মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। ‘শাফা’আহ’-এর নীতি অনুযায়ী, তার ভোটের ফলে অর্জিত সওয়াব বা গুনাহ তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে । যদি একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে তাদের এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য নেতাদের নির্বাচিত করে, তবে এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য তারা সম্মিলিতভাবে দায়ী হবে, যা তাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারে।
সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট নিছক একটি রাজনৈতিক অধিকার নয়, বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এটি একই সঙ্গে একটি পবিত্র আমানত, যা যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করতে হবে; যা সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে; এবং একটি সুদূরপ্রসারী সুপারিশ, যার ভালো-মন্দের অংশীদারিত্ব ভোটারকে ইহকাল ও পরকালে বহন করতে হবে। এই তিনটি ধারণা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সম্মিলিতভাবে একটি একক ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে।
অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তার ভোটাধিকারকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা ও বিচার-বিবেচনার সঙ্গে তা প্রয়োগ করা। একটি সঠিক ভোট যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে, তেমনি একটি ভুল ভোট পাপ অর্জন এবং সমাজে অন্যায় ও দুর্নীতি প্রসারের কারণ হতে পারে। চূড়ান্ত বিচারে, প্রতিটি ভোটের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।